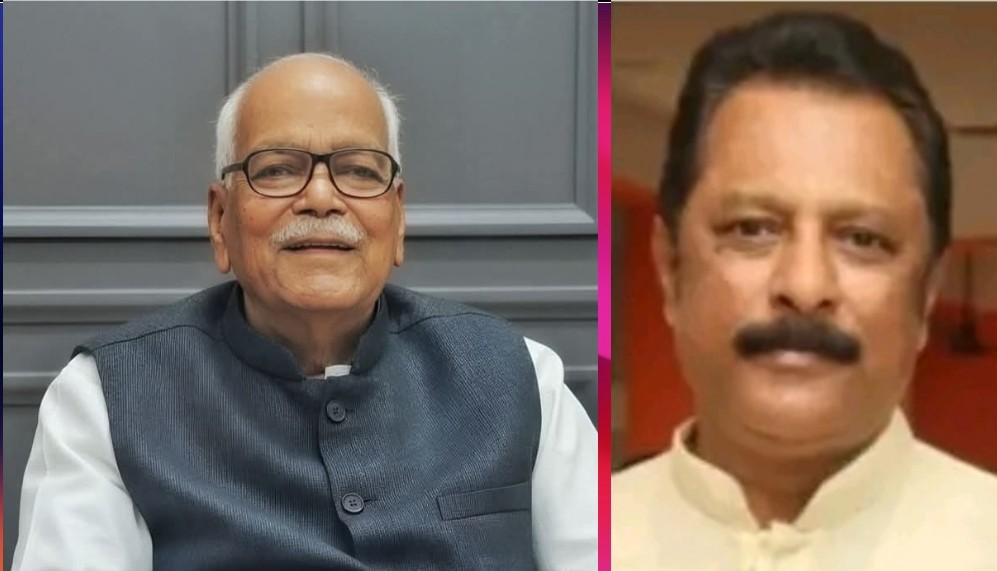।। প্রদীপ দত্ত রায়।।
(লেখক প্রাক্তন ছাত্রনেতা ও গৌহাটি হাইকোর্টের আইনজীবী)
২১ নভেম্বর : শিক্ষা, রাজনীতি, সমাজসেবা এসব মিলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী আবুল কালাম আজাদ বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তার মূল নাম আবুল কালাম গুলাম মহিউদ্দিন কিন্তু তিনি মাওলানা আজাদ নামেই পরিচিত ছিলেন। ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে আজীবন অবিচল ছিলেন তিনি। স্বাধীনতার প্রাক্কালে সীমান্ত গান্ধী খান আব্দুল গফুর খান , মহাত্মা গান্ধী এবং মওলানা আজাদ দেশভাগের বিরোধী ছিলেন এবং তারা ধর্মনিরপেক্ষ নীতিকে আঁকড়ে ধরে দেশ স্বাধীন হোক সেটাই চেয়েছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতা লর্ড মাউন্টব্যাটেনের টোপ গিলে দেশভাগের পক্ষে চলে গেলে বিভাজন ঠেকানো যায়নি। কংগ্রেসের তাবড় তাবড় নেতারা মুসলিম লিগের মতোই দেশভাগের পক্ষে চলে গেলে আজাদের পক্ষে দেশবাসীকে বিভাজনের বিরুদ্ধে এককাট্টা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে সে সময়ে মহাত্মা গান্ধী তার দুই প্রিয় জহরলাল নেহরু এবং মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কাউকেই অসন্তুষ্ট করতে চাননি। সেই সন্ধিক্ষণে গান্ধীজিও দেশভাগ নিয়ে নিরব হয়ে যান। যদিও এর আগে তিনি ঘোষণা করেছিলেন দেশভাগ তার দেহের উপর দিয়ে হবে। কিন্তু দেশভাগ হয়েছে। আর এই দেশভাগের যন্ত্রণা মওলানা আজাদকে খুবই কষ্ট দিয়েছে। তিনি ভারতের হাজার বছরের ইতিহাস তুলে ধরে বলেছিলেন যে হিন্দু এবং মুসলিম এই দেশে একসঙ্গে সহাবস্থান করে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও করে থাকতে সক্ষম। কেবল বক্তব্যই নয় তার আচরণেও সব সময় দেশপ্রেম, ধর্মনিরপেক্ষতা, ন্যয় এবং স্বাভিমান লক্ষ্য করা যায়। দেশভাগের পর দিল্লির জামা মসজিদে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ক্ষুব্ধ আজাদ বলেছিলেন দ্বিজাতি তত্ত্ব আমাদের আস্থা এবং বিশ্বাসে মৃত্যুর পেরেক পুতে দিয়েছে। ১৯৩৯ সালে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ফের কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হন এটা চাইছিলেন না মহাত্মা গান্ধী। ফলে তিনি কংগ্রেস সভাপতি পদে আজাদের নাম ঘোষণা করেন। কিন্তু আজাদ দেখলেন নেতাজির বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা উচিত কাজ হবে না তাই তিনি নিজেই সরে দাঁড়ান। এই ঘটনাই দেশের প্রতি আজাদের দায়বদ্ধতার দিকটি তুলে ধরে।
সিপাহী বিদ্রোহের পর মওলানা আজাদের বাবা মওলানা খায়রুদ্দিন মক্কায় চলে যান এবং সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। খায়রুদ্দিনের পূর্বপুরুষরা আফগানিস্তানের হীরা শহরে বসবাস করতেন। বাবরের রাজত্বকালে তারা বঙ্গদেশে চলে আসেন। কলকাতায় বসবাস করতে থাকেন। খাইরুদ্দিন আরব মহিলাকে বিয়ে করে মক্কায় বসবাস করাকালীন ১৮৮৮ সালে ১১ নভেম্বর মৌলানা আবুল কালাম আজাদের জন্ম হয়। মৌলানা খাইরুদ্দিন ১৮৯০ সালে মক্কা ত্যাগ করে কলকাতায় ফিরে আসেন। কলকাতায় মাওলানা আজাদের ইসলামিক শিক্ষা শুরু হয়। কারণ, তার পরিবার ছিল গোড়া মুসলমান। গৃহ শিক্ষকের কাছেই তার পড়াশোনা, যেমনটা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ক্ষেত্রে। ইসলামিক শিক্ষা গ্রহণ শেষ হওয়ার পর আজাদের বাবা তাকে অন্যান্য বিষয়ে পড়ানোর জন্য বিশিষ্ট শিক্ষকদের নিয়োগ করেন। ইসলামিক শিক্ষা ছাড়াও আজাদ আরবি, পার্শিয়ান, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষা শিক্ষার পাশাপাশি ফিলোসফি, গণিত, জ্যামিতি , আলজেব্রা, বিশ্ব ইতিহাস, রাজনীতি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। পড়াশোনার প্রতি তার এতই আগ্রহ ছিল যে তিনি যে কোনো বিষয়কে খুব ভালোভাবে অধ্যয়ন করতে পারতেন। তিনি পরবর্তীকালে নিজে নিজেই বিভিন্ন বিষয়ের উপর যথেষ্ট পড়াশোনা করেছেন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়কে হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ্য হয়েছেন। তিনি অজস্র লেখালেখি করেছেন এর মধ্যে কোরআনের আয়াতগুলির ব্যাখ্যা অন্যতম। আজাদের বাবা একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তার আদর্শেই মৌলানা আজাদ ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেকে সম্পূর্ণ শিক্ষিত করে তোলার পথে অগ্রসর হন। তিনি মনে পড়ে বিশ্বাস করতেন শিক্ষাই একজন মানুষকে সম্পূর্ণ করে তুলতে সক্ষম। এর কোনও বিকল্প হতে পারে না।

মওলানা আজাদকে আফগানিস্তান এবং আলীগড়ের ইসলামিক চেতনা তাকে খুব উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল। তিনি এ বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠেন এবং আফগানিস্তান, ইরাক, মিশর, সিরিয়া এবং তুরস্কের যান। ওই সব রাষ্ট্রে যে বিপ্লবী আন্দোলন চলছিল সে বিষয় তাকে আকর্ষণ করে। ইরাকে তার সঙ্গে ইরানের দেশান্তরিত বিপ্লবীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তাদের সঙ্গে আলোচনার মধ্য দিয়ে তার ভিতরেও একটা জাতীয়তাবাদের চেতনা গড়ে ওঠে। তিনি চিন্তা করেন, ওই সব দেশের মানুষ যদি স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করতে পারে তাহলে ভারতের মানুষ কেন তা করতে পারবে না। মিশরে তিনি শেখ মোহাম্মদ আব্দুল এবং সৈয়দ বাসার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আরব দুনিয়ায় যে বৈপ্লবিক কাণ্ডকারখানা চলছে সে বিষয়ে অবগত হন। তবে তিনি সবচেয়ে বেশি অনুপ্রেরণা লাভ করেন তুরস্কের ইয়ং ব্রিগেডের কাজকর্ম দেখে। দেশে ফিরে এসে তিনি তখন বাংলার প্রখ্যাত বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ এবং শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ব্রিটিশ শাসন অবসান কল্পে তিনি তাদের সঙ্গে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন। আজাদ দেখতে পান বিপ্লবী কর্মকান্ড বাংলা ও বিহারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। এই বিপ্লবী চেতনাকে সারা ভারতে ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন উপলব্ধি করেন তিনি। সে অনুযায়ী তিনি গোটা উত্তর ভারত এবং পশ্চিম ভারতে বাংলার বিপ্লবী চেতনা ছড়িয়ে দিতে কাজকর্ম শুরু করেন। কিন্তু ওই সময় তার কাজের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় একাংশের সাম্প্রদায়িক চেতনা। হিন্দু বিপ্লবীদের একাংশ মুসলমান বিরোধী মনোভাব পোষণ করতেন। কারণ , তাদের ধারণা ছিল মুসলমানদের ভরসা করা যায় না। তাদের ধারণা ছিল ব্রিটিশরা মুসলমান সম্প্রদায়কে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপক্ষে ব্যবহার করছে। মুসলমানরা ব্রিটিশের সেই ফাঁদে পা দিয়ে চলছেন। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ অসফল হওয়ায় মুসলিম জনগোষ্ঠীর মানুষ প্রায় আত্মকুপনের মতো পরিস্থিতিতে ছিলেন এবং তাদের মধ্যে আস্থার সংকট দেখা দেয়। ওই সময় স্যার সৈয়ীদ আহমেদ খান সহ কিছু মুসলমান নেতা মুসলিমদের আত্মবিশ্বাস অর্জনের জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। তারা মুসলিমদের সক্রিয় রাজনীতির আসর থেকে দূরে থাকতে এবং শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে নীতি গ্রহণ করতে পরামর্শ দেন। মওলানা আজাদ এ বিষয়টি জানতে পেরে তার মতামত প্রকাশ করে বলেন এটা কেবল দেশপ্রেম হীনতায় নয় এটা ইসলামবিরোধী। কারণ ইসলামে ঈমানের অঙ্গ হলো দেশ প্রেম। কাজী মুসলিমদের দেশের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করতেই হবে। তিনি অনুভব করেন স্বাধীনতা না পেলে মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রগতি সম্ভব নয়।
হিন্দু এবং মুসলিমরা মিলে একসঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রাম করা সম্ভব নয়। মওলানা আজাদ এই ধারণা ভেঙে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট তৎপরতার সঙ্গে কাজ করতে থাকেন। একদিকে যেমন তিনি হিন্দু বিপ্লবীদের সঙ্গে মুসলমান বিপ্লবীদের সংযোগ ঘটিয়ে দেন, অপরদিকে যে মুসলমানরা বিপ্লবী কর্মকাণ্ড থেকে দূরে সরে ছিলেন তাদের কাছে টেনে আনেন। মুসলমানদের তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করে তোলেন। তিনি এই নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন যে এই দেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটাতে হলে হিন্দু মুসলিমকে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে হবে। কারণ, আন্দোলনকারী শক্তি যদি বিভাজিত হয়ে পড়ে তাহলে লক্ষ পূরণ সম্ভব নয়। দেশের হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে যদি ভাতৃত্ববোধ গড়ে না উঠে তাহলে স্বাধীনতা আন্দোলন সফল হওয়া কঠিন, এটা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।তিনি তার লক্ষ্যে যথেষ্ট সফল হয়েছিলেন। তার কাজের পদ্ধতি এবং রাষ্ট্রপ্রেম সম্পর্কে কারো মনে তখন কোনো ধরনের সংশয় ছিল না। স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে তিনি ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। ব্যাপক হারে গড়ে তুলেছেন জনসংযোগ।
সাধারণ মানুষের মধ্যে জাতীয় চেতনা গড়ে তোলার জন্য তিনি ১৯১২ সালে সাপ্তাহিক উর্দু সাময়িকী প্রকাশ করেন। আল হিলাল নামের এই সাময়িকীতে মুসলমান জনগোষ্ঠীকে বিপ্লবের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলার জন্য রচনাবলী স্থান পেত। এর পাশাপাশি হিন্দু মুসলিম ঐক্য স্থাপনের জন্য অনুপ্রেরণা সৃষ্টিকারী লেখনি এতে প্রকাশ পেত। মাত্র ২৪ বছরের যুবক আজাদ পত্রিকা প্রকাশনার মাধ্যমে বিপুল জনমত গঠনে লেগে যাওয়ার পর ব্রিটিশরা চিন্তিত হয়ে পড়ে। বলতে গেলে এই আল হিলাল বিপ্লবীদের মুখপাত্র হয়ে ওঠে । ব্রিটিশ সরকার যখন দেখলো এই পত্রিকাটি বিচ্ছিন্নতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে দেশবাসীকে সরকার বিরোধী অবস্থানে নিয়ে যাচ্ছে তখন ১৯১৪ সালে পত্রিকাটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দেয়। তবে এই পত্রিকা বন্ধ করে দিল মৌলানা আজাদ ফের আল বালাদ নামে আরেকটি পত্রিকা শুরু করেন। ওই পত্রিকাতেও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের গড়ে তোলার মিশনকে সামনে রেখে কাজ করতে থাকেন। হিন্দু মুসলিম ঐক্যকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য এই পত্রিকা অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করতে থাকে। তার এই পত্রিকা জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি হওয়ায় ব্রিটিশ শাসকরা চিন্তিত হয়ে পড়ে এবং ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে এই পত্রিকাটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। কেবল তাই নয় মাওলানা আজাদকে কলকাতা ছাড়তে বাধ্য করে এবং তাকে রাঁচিতে গৃহবন্দী করে রাখে। ১৯ ২০ খ্রিস্টাব্দে মৌলানা আজাদ সেখান থেকে মুক্তি লাভ করেন।
১৯২০ খ্রিস্টাব্দেই মৌলানা আজাদ কংগ্রেসের যোগ দেন এবং মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়েন। ওই ওই সময় তিনি তুরস্কের ব্রিটিশ শাসনের অবসানের জন্য মুসলিম কমিউনিটিকে নিয়ে খিলাফত আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে দিল্লিতে আয়োজিত কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন। কংগ্রেসের হয়ে তিনি সারা দেশে আন্দোলনের কর্মসূচি ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে যুক্ত হয়ে পড়েন। গান্ধীজীর নেতৃত্বে তার আস্থা গড়ে ওঠে কারণ গান্ধীজী সাম্প্রদায়িকতা এবং জাতপাতের ঊর্ধ্বে ছিলেন। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে লবণ সত্যাগ্রহে অংশ নিয়ে মাওলানা আজাদ গ্রেপ্তার হন। তাকে মিরাট জেলে দেড় বছর আটকে রাখা হয়। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে রামগড় অধিবেশনে তিনি কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন। ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত তিনি এই পদে বহাল ছিলেন। তার অসাম্প্রদায়িক চেতনার জন্যই কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ তাকে এই পদে নির্বাচিত করে দলের কাজকর্মকে আরো জনমুখী করে তোলার চেষ্টা করেছিল। কংগ্রেস সে সময় ‘ভারত ছাড়ো ‘ আন্দোলনসহ রান্না কর্মসূচি রূপায়ণ করেছে। বলতে গেলে এই সময়ে স্বাধীনতা আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। মওলানা আজাদ দেশের বিভিন্ন প্রান্তের কংগ্রেস নেতাদের দেশভাগ ঠেকানোর জন্য আন্দোলনে শরিক হতে আহ্বান জানান। কারণ, তখন কংগ্রেস ছিল একমাত্র রাজনৈতিক দল যার চরিত্র ছিল ধর্মনিরপেক্ষ।
১৯৫৮ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি মওলানা আজাদ প্রয়াত হন। ১৯৫৮ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি সংসদে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু তার প্রতি যে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেছেন এতেই ফুটে ওঠে তার ভারতীয় রাজনীতিতে স্থান ছিল কত উঁচুতে। মওলানা আজাদকে তিনি অদ্ভুত এবং বিশেষ ধরনের মহত্ত্বের প্রতীক হিসাবে বর্ণনা করেন। নেহরু বলেন, ‘আজ হামারা মির ই কারোওয়ান চালা গয়া’। এটা খুবই দুঃখের ব্যাপার। তার মত এত বড় মহান নেতা ভারতে হয়তো আর জন্মগ্রহণ করবেন না। এই মূল্যায়ন খুবই হৃদয়স্পর্শী। দেশের ইতিহাসবিদরা মওলানা আজাদের কর্মকাণ্ড নিয়ে যত গবেষণা করেছেন ততই অবাক হয়েছেন। ভারতের প্রাথমিক, মাধ্যমিক, বিজ্ঞান শিক্ষার বিকাশে তার যে চেতনা ছিল তা অকল্পনীয়। তার উদ্যোগেই আইআইটি, আইআইএম এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন গঠিত হয়। দেশের বয়স্কদের শিক্ষার জন্য এডাল্ট এডুকেশন বোর্ড তারই পরামর্শে গঠিত হয়। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ভারতের শিক্ষা এবং সংস্কৃতির আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে তার যে চিন্তা ধারা ছিল সেটা খুবই সুদূরপ্রসারী। ভারত এর সুফল পেয়েছে। এই মহান ব্যক্তিকে ১৯৯২ সালে মরণোত্তর ভারতরত্ন সম্মান প্রদান করে তার যোগ্যতার যথার্থ মূল্যায়ন করা হয়।
(মতামত লেখকের ব্যক্তিগত)